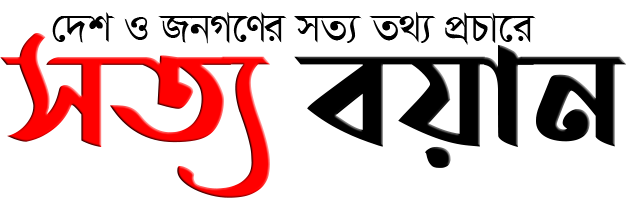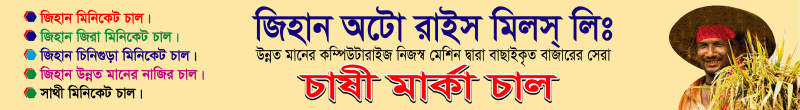ঝড় এলো এলো ঝড়
আম পড় আম পড়
কাঁচা আম ডাঁসা আম
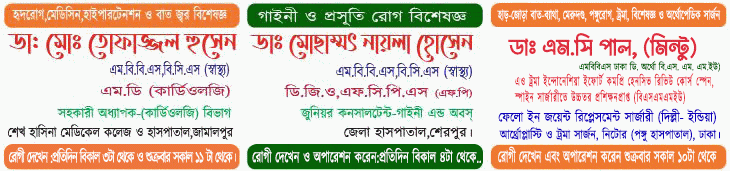
টক টক মিষ্টি
এই যা-
এলো বুঝি বৃষ্টি।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখন বিটিভি রঙিন হলেও আমাদের বাসার তথা পাড়ার টিভি সাদা কালোই ছিলো। ফেরদৌসী রহমান এতই দরদের সাথে গান শেখাতেন যে, উত্তরের মফস্বল শহরের শিশুরাও অসুরে সুরে গাইতাম-
আতা গাছে তোতা পাখি, বুলবুল পাখি ময়না, নাচো তো দেখি আমার পুতুল, মোমেরো পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে যায়সহ আরও কত কত গান। তবে ঝড় এলো এলো ঝড় সম্ভবত সবচেয়ে প্রিয় ছিলো আমাদের।
কেন?
রবিঠাকুরের শৈশবের সাথে না ফেরদৌসী রহমানের শৈশবের সাথে আমাদের শৈশব একাকার হয়ে যেত তা আমাদের জানা নেই। আজ বুঝি এই ইট-কাঠের নগরী বানাতে গিয়ে, তাদের অধিক নিরাপদ করতে গিয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের শৈশবকে চিরকাকালীন কিছু আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছি। সকলে মিলে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা ভাগ করে নেওয়ার স্মৃতিহীন করে তুলেছি তাদের। এখন যতই তাদের শেখাতে চাই না কেন সাম্যের বাণী, তারা কী করে তা বুঝবে তা আমি জানি না। এ লেখা তাই সেইসব পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা- যারা আমাদের মাতৃত্বের, পিতৃত্বের দায় বহন করতে গিয়ে চিরকালীন শৈশববঞ্চিত হয়ে ফ্ল্যাট বন্দি বা গৃহবন্দি।
টুপটাপ পড়ে আম
পিছনে ও সামনে
চট করে গুটিকয়েক
ডাঁসা ডাঁসা আম নে
রবীন্দ্রনাথের ও ফেরদৌসী রহমানের আমগাছ আমবাগানে ছিল নাকি বাসার সীমানা ঘেরা দেয়ালের ভেতরে ছিল তা আমি জানি না, আমার তিন থেকে পাঁচ বছর বয়স কালে তিনটি আমগাছ ছিল বাসার সীমানার ভেতর। যার একটিতে আমের মুকুল তথা মঞ্জরি ধরত না, সেটা নাকি পুরুষ গাছ। বহুবার সেই গাছ কেটে ফেলার কথা উঠলেও কাটা হয়নি। সেই গাছে উঠে ডালে ডালে আমি, ছোট ভাই ও আমার বন্ধুরা শুয়ে থাকতাম পাখি হয়ে, বাঁদর হয়ে। আমাদের জানা-শোনার ভেতর নজরুলের কাঠবিড়ালী ব্যতীত কোনো কাঠবিড়ালী ছিল না, থাকলে আমরা কাঠবিড়ালীও হতাম কি? তবে এক দুপুরে গাছের ডালে এক বিড়ালকে শুয়ে থাকতে দেখে আমরা সেটাকেই কাঠবিড়ালী বানিয়ে বিশাল হৈচৈ করেছিলাম, তা মনে আছে। সীমানার ভেতরে তিনটি আমগাছ, একটি ছাতিম গাছ, একটি নিমগাছ, একটি শিউলী গাছ, ক’টি সুপারি গাছ, বাইরে দুটি আমগাছ, একটি আতা গাছ, বাসা থেকে কিছু দূরে একটি আমড়াগাছ হচ্ছে আমার শৈশব। বাসার পেছনের জঙ্গলের নাম না-জানা গাছগুলো ছিল, একদিন আমিও আফ্রিকার জঙ্গলে অভিযানে যাব এর প্রস্তুতি। তবে স্বর্ণালুর হলুদফুল কখন বাঁদরলাঠি হতো, কীভাবে হতো- তা ছিল আমাদের জানার বাইরে। যেমন জানার বাইরে ছিল আমের মুকুল তথা মঞ্জরি কী করে আম হতো। অবশ্য দৃশ্যমান আম হয়ে ওঠার পর আমাদের আর মঞ্জরি নিয়ে মাথাব্যথা তেমন থাকত না। আমরা অপেক্ষা করতাম ঝড়ের। একটু বড়রা ঝিনুক ঘষে আম ছিলার অস্ত্র বানাত।
আমরা কি ঝড়ের অপেক্ষাতেই বসে থাকতাম? না, অবশ্যই নয়। ঢিল মারার জন্য পৌরসভার রাস্তা বানানোর পাথর আমাদের সংগ্রহে থাকত, বাড়ি বানানোর খোয়া বা ইটের টুকরোও থাকত। সেসব না থাকলে মাটির দলা খুঁজে পেতে খুব কষ্ট হতো না। তবে ঝামেলা হচ্ছে ঢিল মারলে আম পড়ুক আর না-ই পড়ুক মা-চাচি কিংবা পাড়াতো খালা, নানির বকাঝকা যে কিছু ঢিলের মতোই আমাদের ওপর বর্ষিত হতো, তা নিশ্চিত। সেই বর্ষণে ভিজতে কিংবা আমরা কে কত বড় ঢিলন্দাজ হয়েছি তা পরীক্ষার জন্যও আমরা ঢিল ছুড়তাম কাঁচা আম লক্ষ্য করে। যার ঢিলে আম পড়ত এবং যে সবচেয়ে সবচেয়ে দ্রুত ছোটে, যে আম নিয়ে আসতে পারত- তার ভাগে কয়েক কুঁচি আম বেশি পড়ত। আর ঝড় উঠলেই মায়ের নিষেধ উপেক্ষা করে গাছের নিচে ছুটে গিয়ে আম কুড়ানোর গল্পটা রবি কাকা কয়েক লাইনেই কি আনন্দে ধরেছেন!
তারপরে দে না ছুট
চল চল জলদি
নইলে যে বৃষ্টিতে
ভিজে হবে সর্দি
আর তাতে হবে অনাসৃষ্টি
এই যা-
এলো বুঝি বৃষ্টি।
না, রবি কাকার মতো আমাদের ‘ভিজে হবে সর্দি’ নিয়ে উদ্বেগ ছিল না, এই উদ্বেগ মায়ের। আমরা বরঞ্চ বৃষ্টি ভিজে আম কুড়াতেই পছন্দ করতাম। কারণও ছিল, বাবার বদলি চাকরির সুবাদে যখন ঠাকুরগাঁও কলোনিতে আমাদের বাস, তখন আমগাছগুলোর ওপর যে আমাদের অধিকার, সেই আমাদেরকে জনগণই বলা যায়, সংখ্যায় তা বিশাল। তো যে আগে ছুটে যাবে, সে-ই আমের মালিক। এখন সব আমরার সাথে সাথে সব ভাগ হয় না। তাই আমরা ও তাহারা। তাহারাও আমাদের মতোই তৎপর, বেশ একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। ততদিনে আমরা একটু বড়ও হয়েছি, কাগজে মোড়ানো লবণ, মরিচ গুঁড়ার সাথে ঝিনুকাস্ত্রের বদলে হ্যাকসো ব্লেড চাকু থাকে পকেটে। কারও কারও পকেটে মেলা থেকে কেনা ভাঁজ করা চাকুও আছে। সবই আম কাটার অস্ত্র। তবে ভয় দেখাতেও বেশ কাজের।
কলোনির বিশাল সীমানা প্রাচীরের বাইরে, তবে নিকটবর্তী পৌর-সড়কের দু-পাশের আমগাছগুলোর আমে অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুরুষতান্ত্রিক শিকারি আমরা বৃষ্টি ভিজেই অভিযান চালাতাম, সীমানার ভেতরে গাছগুলো মেয়েদের জন্য ছেড়ে দিয়ে আমরা সব ভালো ছেলে।
তবে সীমানার ভেতরে লিচুগাছ, জামগাছ, বরইগাছ, বাতাবিগাছ, বেলগাছের শাসনভার আমাদের হাতেই। পৌর-সড়কের পাশে এসব গাছ ছিল না যে। তবে সমস্যা পাকাতেন বাবা-মায়েরা তথা বড়রা, তারা সবজি ও ফুলচাষের অজুহাতে তার কিংবা বাঁশের বেড়া দিয়ে বাসার আশপাশ দখলে নিয়ে নেন, তাতে কোনো না কোনো ফলবান গাছ তাদের দখলে চলে যায়। তাই ঝড় নামক খোদাই বণ্টন ব্যবস্থায় আর আমাদের কোনো সুযোগ থাকে না, আমরাও তাই সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রাচীন মানবিক উপায়- ‘অধিকার লড়ে নিতে হয়, অধিকার চুরি করে নিতে হয়’- পথে হাটি। ততদিনে আমরা জেনে গেছি- চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা। তাই ধুরন্দর চোরেরা সাধু বেশে, বখাটেরা সাধারণ চোর।
গাছের ফল মাটিতে পড়ে ছাগলে খেলেও সাধারণেরা ধরা, আর যখন গভীর তদন্তেও সঠিক চোরকে ধরা যাচ্ছে না তখনও তারা ধরা। তবে বখাটে চোরদের ইমান খুবই শক্ত, কঠোর সাজাতেও তারা মুখ খোলে না। আর ছিল মধ্যবিত্ত চোর, বেচারারা নিরীহসাধারণ, ‘সঙ্গ দোষে লোহা বায়’ এর কিশোরাকৃতি। কখন তাদের নাছোড় উপস্থিতি কখন মুখোশ হিসেবেই তাদের নেওয়া হতো। ধুরন্ধর ও মধ্যবিত্ত উভয় চোরই স্কুলের ভালো ছাত্র, কলোনীর সবচেয়ে ভদ্র ছেলেদের তালিকাভুক্ত। শাসকশ্রেণি বা বড়দের বিভ্রান্ত করতেই মধ্যবিত্তদের চুরিতে শামিল করা হতো তখনই, যখন চুরির উদ্দেশ্য শুধু ফলাহার নয়, শাসকদের মেসেজ দেওয়াও যে সীমানা বেড়া আমরা মানি না। প্রথমে চুরি করা হতো, তারপর মধ্যবিত্ত চোরের হাতে দিয়ে ‘চিরবঞ্চিত’ মেয়েদের কাছে চুরির ফল ভাগ দেওয়া হতো। অবশ্য তাদেরও কিছু কাজ থাকত, যেমন- আম হলে সেটা চাটনি বানানো, বাতাবি হলে তা ছিলে মাখানো, বেল হলে তা দিয়ে শরবত জাতীয় কিছু বানানো। এসব ভাগাভাগি ও অন্যান্য কর্মযজ্ঞ চলত সাধারণত ছাদে, সিঁড়িঘরের ছাদে। ক’দিন পর মেয়েদের আলাপ সূত্রে চোর ধরা পড়ত এবং শাসকগোষ্ঠী নিরীহ ও সজ্জন মধ্যবিত্ত সেরা স্কুলছাত্রটিকে চোররূপে দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। তাকে রিমান্ড ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হতো। অধিকাংশ সময়েই তাকে কোনো জেরাই করা হতো না, মাঝে মাঝে মৃদু জেরায় সে অবশ্যই বখাটেদের নাম বলত এবং সঙ্গে এটাও জানাত যে, ওই গাছের মালিক সমিতির কোন সদস্য কোনকালে কোন অন্যায্য কথাটি বলেছে।
আর বালিকা বিবর্জিত চুরি বা সিরিয়াস চুরিতে ধুরন্ধর ও বখাটে ঐক্য পরিষদ জিন্দাবাদ। ভাগাভাগি হতো বিশাল খোলা গ্যারেজের স্তূপীকৃত বিদ্যুৎ বিভাগের খাম্বার আড়ালে, সেখানেই ভোজন শেষ হতো, তবে কখন কখন চুরির মাল বেশি হয়ে গেলে আমরা বিভিন্ন সুইস ব্যাংকে জমা রাখতাম। আমাদের সবচেয়ে পছন্দের ব্যাংক ছিল ছাদের পানির ট্যাঙ্কের নিচের ফাঁকা জায়গা।
সর্দিটা হলে ভাই
আম খাওয়া বন্ধ
কাঁচা হোক ডাঁসা হোক
সবটাই মন্দ।
তার চেয়ে চল যাই
করি কিছু খাটনি,
নুন-ঝাল-তেল মেখে
করে নিই চাটনি।
ঠাকুরগাঁও কলোনি শেষে আমরা যখন রাজশাহী সপুরার কলোনিতে এলাম, তখন সেখানে খেলার মাঠের পাশে একটা ছোট আমবাগানোও পাওয়া গেল। তো ঝড় বৃষ্টি এলে তাতে ছেলেতে মেয়েতে বেশ ছোটাছুটি হতো, বড় যে হচ্ছিলাম। চাটনি বানানো ও তা মিলেমিশে খাওয়ার অন্য এক মানেও দাঁড়াচ্ছিল তখন। তবে রাজশাহী কলোনির সেরা পাওয়া দুটি পুকুর ও পুকুর ঘিরে ডাবগাছের সারি। শবেবরাত কিংবা অনুরূপ প্রার্থনার রাতে দক্ষরা গাছে উঠে যেত, ক্রিকেট উইকেট কিপাররা ততোধিক দক্ষতায় ডাব ক্যাচ ধরত। যে ক’টা পারা যায় গলাধঃকরণ করে বাকিগুলো পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হতো খাওয়াগুলিসহ। তবে অখাওয়াগুলি ইটের টুকরো বেঁধে একটু ডুবিয়ে রাখা হতো যেন বড়দের চোখে না পড়ে। পরদিন বা পুকুরে দল বেঁধে গোসলের কালে পুকুরের জলের সাথে ডাবের পানি পান।
কি যে মজা চাটনিতে
টক-ঝাল-মিষ্টি,
দেখলেই জিভ পুরে
আসে পানি বৃষ্টি,
আহা কি যে মিষ্টি মিষ্টি
এই যা-
এলো বুঝি বৃষ্টি।
আরও একটু বড় হলে আম কুড়ানোর ছোটাছুটিটা ছোটদের জন্য রেখে আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে লাগলাম।